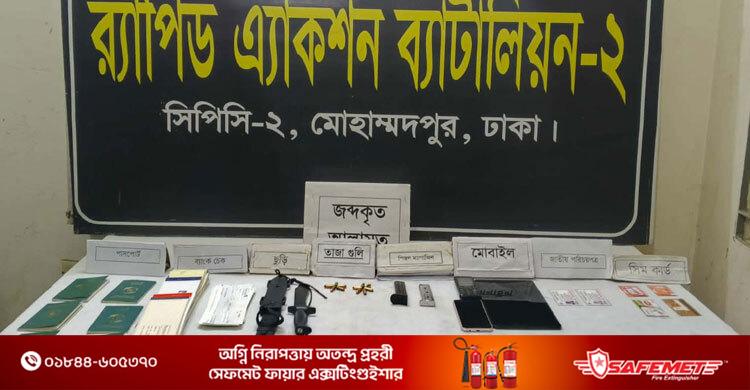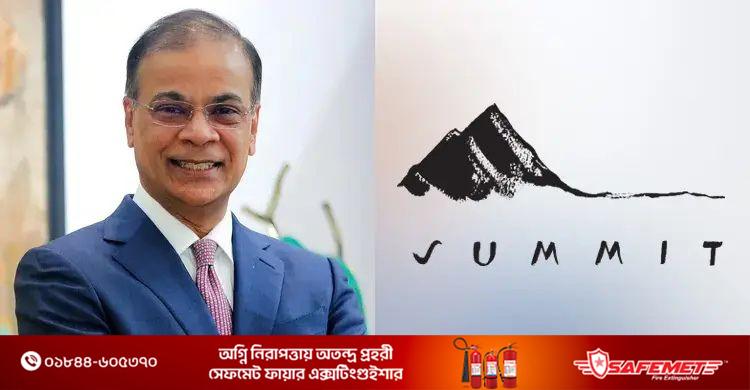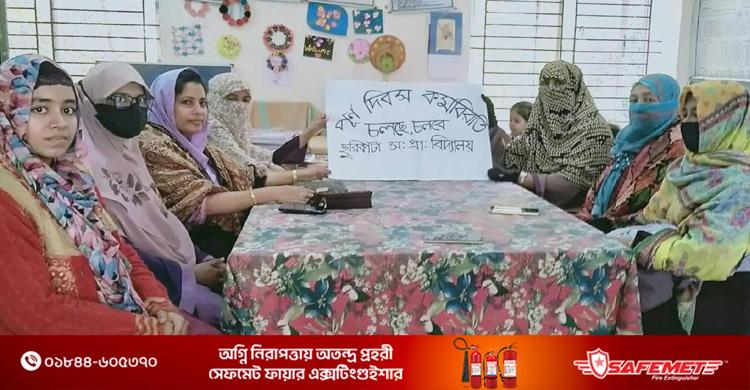এত
সব
উদাহরণ
থেকে
এটা
পরিষ্কার
যে
বাংলাদেশের
জন্য
তার
সংবিধান
সংস্কারের
যে
সুযোগ
এসেছে,
সেটা
বাস্তবায়নের
জন্য
তার
সামনে
অনেকগুলো
পথ
খোলা
আছে।
অন্তর্বর্তীকালীন
সরকারের
অধ্যাদেশ,
সাংবিধানিক
পরিষদ,
সংবিধান
সংস্কার
পরিষদ,
এক
নির্বাচনে
সাংবিধানিক
পরিষদ
এবং
সংসদ,
কেবল
সংসদ
এবং
গণভোট;
সব
পথেই
সংবিধান
সংস্কার
সম্ভব।
অনেকেই
মনে
করেন
যে
সাংবিধানিক
পরিষদ
সৃষ্টি
হলে
সংবিধান
নতুন
করে
লেখার
চাপ
সৃষ্টি
হবে
এবং
দেশ
অস্থিতিশীল
হয়ে
উঠবে।
আমরা
অন্য
দেশের
উদাহরণ
থেকে
দেখলাম
যে
সংবিধান
সংস্কারের
জন্যও
সাংবিধানিক
পরিষদের
নির্বাচন
করা
যায়;
সুতরাং
সাংবিধানিক
পরিষদ
সৃষ্টি
করলেই
চলমান
সংবিধান
বাতিল
হয়ে
যায়
না।
অতএব
নতুন
সংবিধান
তৈরির
প্রশ্ন
ওঠে
না।
বাংলাদেশের
ক্ষেত্রে
সাংবিধানিক
পরিষদ,
সংবিধান
সংস্কার
পরিষদ
বা
সংসদ,
সব
ক্ষেত্রেই
ঐকমত্য
সনদের
ভিত্তিতেই
সংস্কার
করবে,
বিধায়
নতুন
সংবিধানের
আবদার
খুব
একটা
হালে
পানি
পাওয়ার
সম্ভাবনা
কম।
বাস্তবায়নের
পথে
আসল
চ্যালেঞ্জ
হচ্ছে
সংস্কার
প্রস্তাবনার
বিষয়ে
কোনো
দ্বিধা
না
রেখে
একটা
ঐকমত্যে
পৌঁছানো।
আপত্তি
নিষ্পত্তি
করে
একটা
পরিষ্কার
প্রস্তাব
দাঁড়
করাতে
পারলে
বাকি
পথ
সহজ
হয়ে
যাবে।
সেই
পরিষ্কার
করার
পথে
সংস্কারের
পরিসর
নিয়ে
ঐকমত্যে
আসাটা
আরও
একটা
বড়
পরীক্ষা।
এখন
পর্যন্ত
যতটুকু
বিষয়ে
ঐকমত্য
পৌঁছানো
গেছে,
সেটুকুতে
অভ্যুত্থান-পরবর্তী
জন-আকাঙ্ক্ষার
প্রতিফলন
নেই।
তার
মানে,
দলগুলোকে
ঐকমত্যে
আসা
প্রস্তাবের
সংখ্যা
বাড়াতে
হবে।


 এডমিন
এডমিন