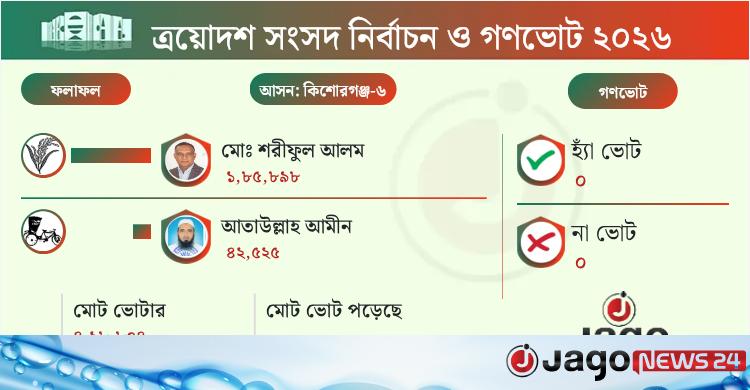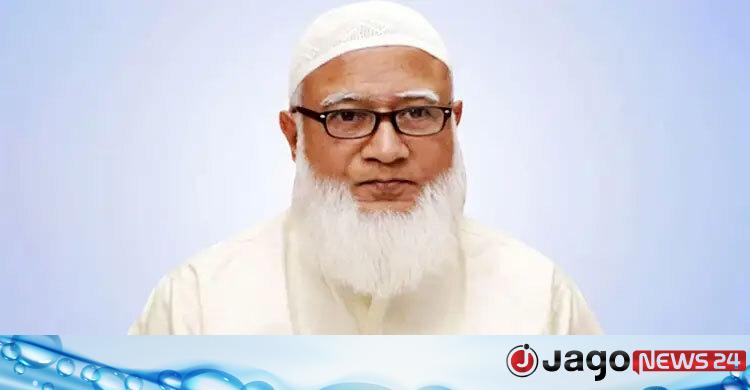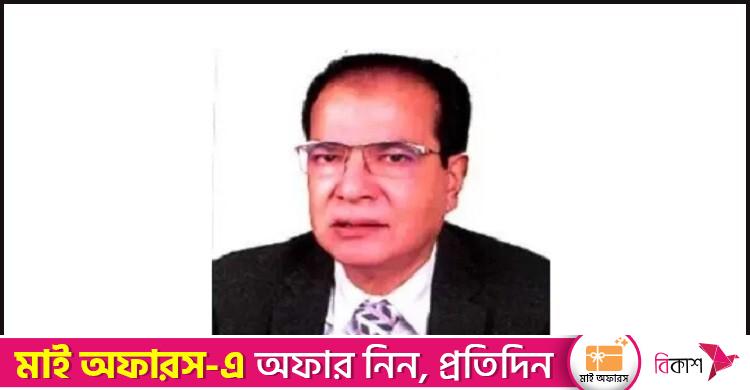স্বাধীনতা–পরবর্তী
রাজনৈতিক-সামাজিক
ঘূর্ণাবর্তের
কালেই
গ্রুপ
থিয়েটার
নাট্যচর্চার
আরম্ভ।
কিছু
মানুষের
ভালো
লাগা
বা
শখ
থেকে
সেটা
শুরু
হলেও,
পরে
তা
আর
শখের
মধ্যে
সীমাবদ্ধ
ছিল
না।
রাজনৈতিক
ঘটনাবলির
নানা
অস্থিরতার
ভেতর
নাটক
একটি
সামাজিক
আন্দোলন
হয়ে
দেখা
দিল।
বাংলাদেশের
মধ্যবিত্তের
কাছে
স্বাধীনতা
লাভের
অর্থ
ছিল,
স্বাধীনতা-পূর্বের
চেয়ে
সচ্ছল
জীবন
এবং
সুখ
ও
সমৃদ্ধি।
স্বাধীন
বাংলাদেশে
কোনো
রকম
অনিশ্চয়তা
চায়নি
তারা,
নিরাপত্তাহীনতায়
ভুগতে
চায়নি।
সামাজিক-রাজনৈতিক
দিক
থেকে
বিশৃঙ্খলা,
সরকারের
স্বৈরাচারী
মনোভাব,
বুদ্ধিজীবী
ও
নেতৃত্বের
দোদুল্যমান
অবস্থা,
চারদিকে
নৈরাজ্য,
খাদ্যাভাব,
দ্রব্যমূল্যের
ঊর্ধ্বগতি,
যুদ্ধোত্তর
সময়ের
স্বাভাবিক
পরিণতি
হলেও
যারা
৯
মাস
যুদ্ধে
নতুন
জীবনের
স্বপ্ন
দেখেছে,
তারা
এই
অবস্থা
মেনে
নিতে
পারেনি।
তারা
কিছু
করতে
চাইল।
তাদের
এই
রাজনৈতিক
চ্যালেঞ্জের
মাধ্যম
হিসেবে
তারা
বেছে
নিল
নাটককে।
বাংলাদেশের
স্বাধীনতাযুদ্ধ–উত্তরকালে
যখন
নাগরিক
জীবন
বিধ্বস্ত,
বিধ্বস্ত
মূল্যবোধ,
প্রত্যেক
মানুষ
ভুগছে
এক
নৈতিক
দ্বন্দ্বে,
প্রায়
অনিবার্যভাবেই
নেমে
পড়েছে
অধঃপতনের
খাদে,
সরকারপক্ষ
যখন
সর্বশক্তি
দিয়ে
বিরুদ্ধ
পক্ষকে
দমন
করতে
উদ্যত,
সাধারণ
মানুষ
যখন
তার
সামনে
অসহায়,
কোথাও
ন্যায়বিচার
নেই,
নাটক
তখন
মধ্যবিত্তের
সান্ত্বনা
ও
সাহস
হিসেবে
তার
পাশে
দাঁড়িয়েছিল।
শোষণ–বঞ্চনার
বিরুদ্ধে
সে
মানুষের
মধ্যে
ক্ষোভ
জাগিয়ে
তুলতে
চেয়েছিল।
যুদ্ধবিধ্বস্ত
বা
যুদ্ধ–পরবর্তী
অবক্ষয়-হত্যা-রাহাজানি-ধর্ষণ—এসবের
বিরুদ্ধে
সরাসরি
লড়ার
শক্তি
বা
অবস্থা
তখন
ছিল
না,
তাই
তাদের
প্রতিবাদ
ঘোষিত
হলো
নাটকের
মধ্য
দিয়ে।
যতটা
প্রতিবাদ,
তার
চেয়ে
বেশি
ক্ষোভ
প্রকাশ।
রামেন্দু
মজুমদার
লিখলেন,
‘আমাদের
তরুণ
তার
ক্ষোভ,
হতাশা,
আশা-আকাঙ্ক্ষা
নিয়ে
পাদপ্রদীপের
সামনে
এসে
দাঁড়াল
অত্যন্ত
দৃপ্ত
পদভারে।’
নাটকের
সংলাপ
হয়ে
উঠল
স্পষ্ট,
তীক্ষ্ণ।


 এডমিন
এডমিন