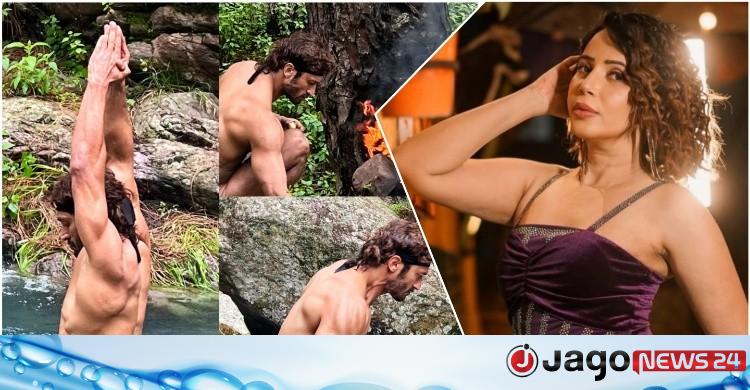বাংলাদেশে
সৈয়দ
ওয়ালীউল্লাহ
কতটা
প্রাসঙ্গিক
আছেন
আজও?
মানে
একাডেমিয়ার
চোখে
নয়,
পাঠকের
চোখে,
তার
সমসাময়িক
যেকোনো
লেখকের
তুলনায়।
‘লালসালু’,
‘কাঁদো
নদী
কাঁদো’,
‘চাঁদের
আমাবস্যা’
বা
‘বহিপীর’—এসব
বই
যদি
এখনো
সাহিত্য
পাঠকের
আগ্রহ
ধরে
রাখে,
তা
কেন
রেখেছে?
ওয়ালীউল্লাহর
রচনা
নিয়ে
অনেক
রকমের
আলাপ
চালু
আছে
বাজারে।
গবেষকেরা
করেন
সেই
আলাপ।
পাঠচক্রগুলোয়
হয়
কথাবার্তা।
কয়েক
প্রজন্মের
শিক্ষার্থীরা
তাঁর
লেখা
পড়ে
চলেছেন
পরীক্ষা
পাসের
জন্য।
এসব
সত্ত্বেও
ওয়ালীউল্লাহ
পাঠ্যপুস্তকের
বর্ণহীন
জগতে
লুপ্ত
হননি
বোধ
করি।
এদিক
থেকে
একাডেমিয়ায়
জায়গা
পাওয়া
আর
যেকোনো
লেখকের
তুলনায়
তিনি
ভাগ্যবান।
এই
প্রাসঙ্গিকতার
অনেক
কারণ
আছে।
যেমন
প্রথম
কারণটি
একই
সঙ্গে
ক্লিশে
ও
তার
অ্যান্টিডোট
দুইই।
এ
সময়ের
গড়
পাঠক
ও
তরুণদের
মধ্যে
একটা
ধারণা
আছে
যে
একবিংশ
শতাব্দীতে
লেখকের
সমাজসচেতনা,
সমাজের
প্রতি
দায়,
ভাষা
ও
টেকনিকের
নিরীক্ষা
এসবের
আর
প্রয়োজন
নেই।
এখন
সময়টা
অর্থহীনতার,
আর
মানুষ
দারুণ
প্রিঅকুপাইড
রিলস,
নিউজফিড,
মেসেঞ্জার,
বা
ওটিটিপিতে
ফিল্ম
স্ট্রিমিংয়ে।
স্যোশাল
মিডিয়া
সবাইকে
বানিয়ে
দিয়েছে
মন্তব্যপ্রবণ।
সবকিছু
নিয়ে
এখন
সবার
মন্তব্য
আছে,
অকাট্যধারণা
আছে
দুনিয়ার
যেকোনো
বিষয়ে।
মানুষ
ভুগছে
মনোযোগজনিত
সমস্যায়ও,
মোবাইল
স্ক্রিনে
অনবরত
ছোট
ছোট
ভিডিও
দেখে
দেখে
তার
ধৈর্যের
স্প্যান
কমে
গেছে।
তাই
এখন
কেউ
জটিল
বাক্যের
দীর্ঘ
টানা
গদ্য
দেখলে
এড়িয়ে
যান,
সমাজ
নিয়ে
নিজের
ধারণা
আহত
হবে
এমন
যেকোনো
কিছুতেও
গড়
মানসে
একটা
আপত্তি
কাজ
করে।
অথচ
ওয়ালীউল্লাহর
সাহিত্য
সহজপাচ্য
কিছু
নয়;
টানা
গদ্য,
জটিল
বর্ণনা,
চেতনার
অবারিত
প্রবাহের
ব্যবহার
আর
সমাজসচেতন
বিষয়বস্তু—তাঁর
লেখায়
সবই
মেলে।
পাশাপাশি
এই
একই
উপাদানগুলো
তাঁকে
মৃত্যুর
পাঁচ
দশক
পরও
নানা
উপায়ে
প্রাসঙ্গিক
রেখেছে।
অর্থাৎ
কাজ
করছে
অ্যান্টিক্লিশে
হিসেবে।


 এডমিন
এডমিন